দ্বিতীয়
পর্ব
প্রশ্ন-১৩) বাক্ ব্লগজিন - একবার আমি এক ব্যক্তিকে একটা বিষয়ে তার পার্টিসিপেসন
চাইছিলাম। লেখা বা কোন মতামত এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে নেই। সে আমাকে বলল, জুবিনকে একটু
জিজ্ঞেস করে নি। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করায় তুমি বললে না খেপুতে তো এরকম কোন নিয়ম
নেই। যে কাউকে কিছু করার আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি ভাবো, মানুষটি কিন্তু
তার থেকে বয়সে অনেক ছোট একজনকে তার অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছে, এই
ক্ষেত্রগুলিতে। মনে হয় না তোমার দায়ীত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। এতোগুলো মানুষের ভরসা
হয়ে উঠতে কেমন লাগে?
জুবিন ঘোষ – এটা এক ধরনের পারস্পরিক
শ্রদ্ধা। কারুর উপর অভিভাবকত্ব বা নতশীলতা নয়। আমাদের সঙ্গের মানুষগুলোকে সবাই
মিলে চেষ্টা করি পরস্পরকে ভরসার স্থানটা দিতে। আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে থেকে এই
প্ল্যাটফর্মটা যতদিন আছে, তাকে
লেখা রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে রক্ষা করার দায়টা আমাদের সবার বলে মনে করি। একদিন
এটাও থাকবে না কালের নিয়মে। নতুন কন প্ল্যাটফর্ম এসে ক্ষেপচুরিয়াসের জায়গা নেবে।
যতদিন আছে, আমরা পরস্পরের ভরসার জায়গা হয়ে থাকি, আমি যেমন এখানে ভরসা পাই,
প্রত্যেকটা মানুষের ভালোমন্দ খবরটা রাখি, অন্যরাও রাখেন। আমরা কেউ একা নিজেরটা নিয়ে থাকি না, এটা
ক্ষেপু সংস্কৃতি। তাঁরাও যে আমায় ভরসা করেন সেটা সত্যি দায়িত্ব তো অনেকটাই বাড়িয়েই
দেয়। দায়িত্বটা কীসের জানো ? –- এতজন অনুজ ও অগ্রজ কবির ভালোবাসার। আর দায়িত্ব বাড়লে জানো তো শক্তিও দ্বিগুণ
হয়। তখন দায়িত্বটাও ভরসার জায়গায় চলে যায়। এই পারস্পরিক ভরসাই আমাকে চাপমুক্ত
লিখতে সাহায্য করে। তাই আমার কোনও ভগবানের দরকার হয় না। এই মানুষগুলোই
ঈশ্বরপ্রতিভূ হয়ে ওঠেন।
প্রশ্ন-১৪) বাক্ ব্লগজিন -
এ শহর থেকে সব দেবী একে একে লীন হয়ে যাচ্ছে দেবলীনা।
এ শহর আমার নয়, তুমিও কি হাঁপিয়ে ওঠোনি ? নিয়ে যাও তেমন কোথাও
যেখানে পড়ে থাকছে মগধের ধুলোর অন্ধকারে,
যেন তুমি — কোনও হারিয়ে
যাওয়া মেগাস্থিনিসের খাতা।
এ শহর চুলোয় গেছে সিগারেটের যাবতীয় ধোঁয়া আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে
;
যেন প্রার্থনা সংগীতের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হ্রাসপ্রাপ্ত
বর্ণাশ্রম থেকে
উঁকি মারে পরাজিত সেলুকাসের ব্যাবিলন।
উঁকি মারে ভুলে যাওয়া আদি-অনন্ত হরপ্পার
নারী, অবিকল সে
হিতৈষিণী অস্ত্রসম্ভবা প্রাচীন ভারত। ছয় লক্ষ সমরবাহিনী
নিয়ে
যে শহর তৈরি থাকে গ্রিক দেবতাদের উচ্ছেদের জন্য ...
আমায় সে শহরে নিয়ে যাও দেবলীনা, যে শহর অযোধ্যার সীতার, ইন্দ্রপ্রস্থের
দ্রৌপদীর স্নিগ্ধতায় বনবাসেও বসবাস করতে পারি। এখন যেখানে
থাকি,
এ শহর আমার নয়, এ আমার অজ্ঞাতবাস। এ শহর তোমারও নয় দেবলীনা
অটো, বাস, কফিশপ, মাল্টিপ্লেক্স, হিপোক্রিট অফিস — দেখে দেখে
হাঁফিয়ে উঠেছি, হাঁফিয়ে উঠেছি অঙ্গসজ্জায়, হাঁপিয়ে থমকে যাচ্ছি
এসকালেটরের সিঁড়িতে।
আবার একটা প্রাচীন সভ্যতা চাই, মহেঞ্জোদাড়োর সুবিশাল স্নানাগার
থেকে
ঝাঁপ মেরে তুলে আনতে চাই দুষ্মন্তের ডুবে যাওয়া আংটি
দেবলীনা, অ্যাটল্যান্টিক বা সুমেরীয়’র মতো এ শহরও
তলিয়ে যাবে
একদিন।
হয়তো আধুনিক সভ্যতা ধ্বংসের পর, প্রাশ্চাত্যের একদল পরিব্রাচক এসে,
খরোষ্ঠী ও জুনাগর লিপিতে, মেডুসার মতো তোমার ওই দু’চোখ
মিথ করে রাখবে কোনও —
মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকায়।
এখানে উত্তম পুরুষ কি জুবিন?
জুবিন ঘোষ – একদম ঠিক ধরেছ। তুমি নিশ্চই
লক্ষ্য করেছ এই কবিতায় ‘আমি’ শব্দটা একবারও নেই, কিন্তু এর প্রতিটার সঙ্গে ‘আমি’টা জুড়ে রয়েছে। এই ‘আমি’ কোনও Lyrical self
নয়, আমার ‘আমি’র চলমান প্রতিবিম্ব। ফরাসি কবি র্যাঁবো-র সেই উক্তির মতো—je est un autre—মানে ‘আমি আর এক’—বহুখণ্ডিত ‘আমি’। এই শহর, এই শহরের নিয়ম কানুন, মানুষের মনোভাব সব যেন
যূপকাষ্ঠ হয়ে উঠছে আমার কাছে। আসলে কী জানো, বঙ্গসংস্কৃতি ঐতিহ্যগুলোকে ইদানীং
সুনিপুণভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তার বদলে একধরনের অপসংস্কৃতির চোরাস্রোত বহিয়ে
দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে ক্রমাগত যাতে একটি বিশেষ শ্রেণির স্বার্থকামীতায় অপসংস্কৃতির
ফলপ্রসূ চিন্তাহীন অসার মানুষগুলোকে ব্যবহার করা যায়। সাম্প্রতিক অতীতটাই তুমি দেখো
না, নয়ের দশকের স্থিরতার সঙ্গে আজকের অস্থিরতা। নয়ের রাজনৈতিক সৌজন্যতা কিংবা
সহনশীলতার সঙ্গে আজকের সৌজন্যতা ও সহনশীলতা, নয়ের সংগীতের আবেদন, স্মরণযোগ্যতার
সঙ্গে আজেকের আবেদন, স্মরণযোগ্যতা; নয়ের সমাজ ব্যবস্থার রীতির সঙ্গে আজকের রীতি
--- বিজ্ঞান এগোলেও গত এক দশকে যুব সমাজের অবক্ষয়ের হারটা সত্যিই লক্ষ্যণীয়। আমি
কিন্তু পালিয়ে যেতে চাইনি, আমি চেয়েছি সমাজটা কমসেকম বিষমুক্ত হোক। মেগাস্থিনিসের
খাতা আসলে একটা অতীত নস্টালজিয়া, পুরোনো ভারতদর্শনের সঙ্গে নতুন ভারতদর্শনের
পার্থক্য বোঝানো। এই ‘আমি’-ও তাই দ্বিধাগ্রস্থ। মাঝে মাঝে মনে হয় আজ যেখানে বাস করছি, এই সময়টা, এমনকি
এই স্থানটাও আমার অজ্ঞাতবাস। সত্যিই কি আমাদের বাংলা এইরকম ছিল ! যেখানে নিজের
শহরকেও অজ্ঞাতবাস বলে মনে হয় !
প্রশ্ন-১৫) বাক্ ব্লগজিন - 'মেগাস্থিনিসের খাতা আসলে একটা অতীত নস্টালজিয়া, পুরোনো
ভারতদর্শনের সঙ্গে নতুন ভারতদর্শনের পার্থক্য বোঝানো' - একটু বুঝিয়ে বলো
এই জায়গাটা?
জুবিন ঘোষ – আমরা প্রত্যেকেই বেড়ে উঠছি
একটা নির্দিষ্ট সামাজিক সীমানার মধ্যে। এই সমাজ ব্যবস্থাটা আজকের নতুন নয়, তা
পরিচালিত হয়ে উঠছে দীর্ঘ সময় ব্যাপী গঠিত ঐতিহ্য ও বহুমান্য বিধানের নির্দেশে। এইগুলোর
লিখিত-অলিখিত পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে বাহিত হয়েই একটা সমাজদর্শন ফুটে ওঠে,
ঐকান্তিক ভারতীয় সভ্যতা সেইরকম কিছু দর্শন তিলে তিলে এর আদিবাসী ও অধিবাসী জনগণের
মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে। মেগাস্থিনিসের খাতা বা ইন্ডিকা আধুনিককালে আর খুজে পাওয়া
যায় না। মেগাস্থিনিস যে ভারতদর্শনের ঠিক কী কী রূপ দেখেছিল সেটা আজ কিছু গবেষকদের
শুধুমাত্র ফুটনোট হয়ে আছে। আসলে আমার এই কাব্যগ্রন্থে পুরোনো ভারতীয় ঐতিহ্যের
সঙ্গে নবভারতকে একটা তুলনা আনা হয়েছে। আজকের অস্থিরতা, অবক্ষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা
করেছি সোনালি অতীতের সাপেক্ষে শ্রীমতি দেবলীনা সেখানে একটা বাহক। যার সঙ্গে
কথাগুলো আদান প্রদান করে নিচ্ছি। তুমি তো জানো, জৈব স্তরে মানুষের চলাচল
প্রবৃত্তির তাড়নায় কাজ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও তার চরিত্র পাল্টেছে। এখন আর
একজনের প্রতি শুধু loyal বা Devotion ব্যাপারটাই খুঁজে পাওয়া দুস্কর হচ্ছে। প্রেম ক্রমশ item হচ্ছে। ফরাসি পারফিউম, বিদেশি টিশার্ট প্রেমকে উসকে দেয়।
ঘুম পেয়েছের মতো প্রেমও আজকাল পায়। প্রেমের অ্যাভলিবিলিটিও বেড়ে যাচ্ছে। মোবাইল
যুগে প্রত্যেকটা ইনফ্যাচুয়েশন এখন মান্যতা পায়। এখন নালন্দা বা বিশ্বভারতীর মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত
শিক্ষাক্ষেত্র নেই, শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিংসাত্মক রাজনীতি। মানুষের
মননশীলতাকে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে সচেতন প্রয়াসে। আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই
একধরনের গিমিক বাসা বেঁধেছে। আজকের যুবসমাজের মধ্যে ডিপ্রেশন অনেক বেশি। কেন জানো?
কারণ গত একদশক আগেও কিন্তু এতটা সামাজিক অবক্ষয়, চিন্তাভাবনার জড়তা ছিল না।
সম্পর্কগুলো অনেক মানবিক ছিল। মেগাস্থিনিসের খাতা আমার আজকের ভারতদর্শন।
প্রশ্ন-১৬) বাক্ ব্লগজিন - বাংলা সাহিত্যে তোমার কন্ট্রিবিউসান কি? ভেবেছো কখনো? খ্যাতি তুমি
ভালোবাসো বলেছ। নিজেকে ঠিক কোন জায়গাটায় দেখতে চাও?
জুবিন ঘোষ – কন্ট্রিবিউশন কি নিজে দেখা
যায় ! অন্যের চোখে দেখতে হয়। তাছাড়া মনে হয় না এই প্রশ্নটা এখনি করার সময় এসেছে।
তবে নিজের লেখা নিয়ে এখন পরীক্ষানীরিক্ষা চালাচ্ছি। হিন্দি সিংহাবলোকন ছন্দকে
বাংলায় ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। আমাকে সাহায্য করেছেন তরুণ কবি ইন্দ্রনীল তেওয়ারী।
এছাড়াও আরও একটি নতুন আঙ্গিককে বাংলা কবিতায় আনবার চেষ্টা করেছি। কিছু কবিতা
লিখেছি। আমার মনে হয় না সেই আঙ্গিক আমার আগে আর কেউ বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন
বলে।
সব’চে ভাল হত রবীন্দ্রনাথ আর
অমিয় চক্রবর্তীর মাঝখানে যদি নিজেকে দেখতে পেতাম। কিংবা বুদ্ধদেব বসু আর
জীবনানন্দের মাঝখানে। সেটা তো হবার নয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য জোকস্, আসল কথা বলি,
মিডিয়ার স্নেহধন্য না হলেও চলবে, সাধারণ পাঠকের স্নেহধন্য হলেই অনেক কিছু পাওয়া
হয়ে যাবে আমার। এমন কিছু লেখা লিখতে চাই যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা মানুষ নিজের
প্রতিফলন পায়। আমার মনের জানলা দরজাগুলো যেন কখনও বন্ধ না হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে
সত্যিই যাতে আমার একটা অন্তত কন্ট্রিবিউশন থাকে একমাত্র সেটাই লক্ষ্য। তাই লেখাতেই
শুধু মন দিচ্ছি। তার জন্য যতটা পরিশ্রম প্রয়োজন ততটা পরিশ্রম করতে আমি রাজি।
প্রশ্ন-১৭) বাক্ ব্লগজিন - বাংলা কবিতায়
নতুন কবিতা আন্দোলনকে কি ভাবে দেখো?
জুবিন ঘোষ – শ্রদ্ধাশীল। এই আন্দোলন
বাংলা কবিতায় নতুন কিছু দিক। তবে একটা সত্যি কথা বলব ? নতুন কবিতা আন্দোলন,
পোস্টমর্ডান কবিতা আন্দোলন, পরিবিষয়ী কবিতা, অতিচেতনাবাদ কবিতা --- এগুলোর মধ্যে
কোনও পার্থক্য করে উঠতে পারছি না। একে-অপরের সঙ্গে আলাদাটা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের
কবিতাকে যেমন রাবিন্দ্রিক বলতে পারি, জীবনানন্দকে আলাদা করতে পারি, হাংরি জেনারেশন
এর সঙ্গে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতাকে পার্থক্য করতে পারি, কিংবা শ্রুতি আন্দলনকে।
একটা পরিবিষয়ী ভাবাদর্শের কবির কবিতা পড়লে সেটাকে পোস্টমর্ডান কবিতার সঙ্গেও মিল
পাচ্ছি, পোস্ট মর্ডানের সঙ্গে নতুন কবিতা আন্দোলনের কবিতার সঙ্গে পার্থক্য আসছে
না। কোনওরকম অশ্রদ্ধা না করেই বলছি, এই বিবিধ আন্দোলন সম্পর্কীত গদ্যগুলোতে ভাবনা
ও মতাদর্শগুলোকে খুব সুচারুভাবে প্রতিফলিত করা হলেও, তার প্রতিফলন কবিতায় পাচ্ছি
না। কোনও কবিতাকে পড়ে ও দেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পাচ্ছি না এটাই পরিবিষয়ী কবিতা,
এটা কোনওভাবে পোস্ট মর্ডানিস্টদের সঙ্গে মিল নেই। আমার তো সব ক’টাকে একসঙ্গে মিলিয়েই নতুন
কবিতা বলতে ইচ্ছে হয়। তবে হ্যাঁ, আমি কবিতা পড়ি, ভালো লাগে। অপেক্ষা করে থাকি নতুন
কবিতার। প্রত্যেকটা আন্দোলনের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাশীল। শুধু চাই, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যতেও
তা যেন অপরাপর আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠুক।
প্রশ্ন-১৮) বাক্ ব্লগজিন - তোমার একটা
স্ট্যাটাস দেখলাম, কোন মহিলা তোমার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। তাতে একজন মতামত
দিতেছেন, মেগাস্থিনিসের খাতার খ্যাতিই এর কারণ। অনেকে সহ্য করতে
পারছে না। তুমি কি বলবে?
জুবিন ঘোষ – আস্তে আস্তে এই
বিড়ম্বনাগুলো তো জড়িয়ে যাবেই জীবনযাত্রার সঙ্গে। তবে বিষয়টা উপভোগ করেছি। আশেপাশে
এইরকম অনেকেই বলবে। উল্টে এগুলো আমার স্ট্যামিনা বাড়িয়ে দেয়। উপেক্ষা ভিন্ন আর
কিছু এদের প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না। আমি কেমন, তা আমার সঙ্গে যারা মিশেছেন
তাঁরা জানেন।
প্রশ্ন-১৯) বাক্ ব্লগজিন - ধর তোমাকে এরকম বলা হল, তুমি কবিতা ছেড়ে যদি সিনেমা বানাও
তাতে বেশি খ্যাতি পাবে, কি করবে?
জুবিন ঘোষ – এমন দুঃসাহস আমার নেই। আর
মনের সুপ্ত ইচ্ছাও নেই। মনের খোরাকের জন্য লিখে যাই, সেটাই বরাবর থাকবে। তুমি আরও
একবার এই প্রশ্নটা করেছ দেখলাম। মৃগাঙ্কশেখর গাঙ্গুলি, পলাশ দে, অনমিত্র রায় থাকতে
আমার সিনেমা বানানোর দরকার নেই, এদের উপরেই আমি ভরসা রাখি। আর জানি এই তরুণ
প্রতিভাবান কবি-পরিচালকরা একদিন মহীরুহ হয়ে উঠবে। আমি কবিতা লিখি। তবে হ্যাঁ সত্যি যদি বানাতে
পারতাম তবে মনের মধ্যে অনেক ভাবনা চলাচল করে, সেগুলো চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে
পারলে ভালোই হত। নির্বাক দৃশ্যের মাধ্যমে দৃশ্যগত কবিতা বানাতাম।
প্রশ্ন-২০) বাক্ ব্লগজিন – আঠারো নম্বর
প্রশ্নটায় যেটা বলতে চেয়েছি, মেগাস্থিনিসের
খাতার পপুলারিটিই কি এর কারণ বলে তোমার মনে হয়? ওই ভদ্রলোক যা দাবি করেছেন।
জুবিন ঘোষ – দেখো, এর পেছনে কোন
ব্যক্তি, কী উদ্দেশ্যে আছে সেটা এখন আর অস্পষ্ট নয়। আমার ভালো লাগছে মেগাস্থিনিসের
খাতা পড়ে ওই ভদ্রলোকের মনে হয়েছে এটাই কারণ। তবে সাদা জামায় কালির ছিটে দিলে দাগ
অনেক স্পষ্ট হয়। সেই চেষ্টা করে পাঠকদের কাছে আমার চরিত্রহনন করার চেষ্টা তো একটা মূল
কারণ তো বটেই। আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে কলঙ্কের দাগ মাখার চেয়ে বরং
আরও কোনও পপুলার পার্সোনালিটিকে বেছে নিলে আখেরে লাভ হত তার।
প্রশ্ন-২১) বাক্ ব্লগজিন -
হিন্দির' ছন্দ' বাংলা কবিতায় আনছ কেন? এটা কেন প্রয়োজন মনে হচ্ছে? আর ওই ছন্দটাই
বা কেন?
জুবিন ঘোষ – হিন্দি ছন্দে অনুপ্রাসের
একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেই ভাষার মাধুর্যের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়।
ইংরেজি Rhyming
Rhyme-এ অনুপ্রাস সুপ্রচলিত। কিন্তু বাংলায় এই
শব্দালংকারটির ব্যবহারে যত গেঁড়া দেখা যায়। বেশ শক্ত। গঙ্গার যেমন টান থাকে, তেমনি
অনুপ্রাসের ব্যবহারের লোভেরও একটা চোরাটান বিদ্যমান। এই টান আমাদের ফাঁদে ফেলে দেয়
আর কৃত্রিম অনুপ্রাসের বাহুল্য কবিতার প্রকরণে উৎকর্ষের বদলে অপকর্ষই বেশি করে। যেখানে বাংলায় অনুপ্রাসের
ব্যবহারের উপরেই চরম সতর্কতা নিতে হয় সেখানে বিশেষ এই হিন্দি সিংহাবলোকন ছন্দ
অনুপ্রাসের উপরেই গড়ে উঠেছে। প্রথম পঙ্ক্তি থেকে শেষ পঙ্ক্তি, এমনকি প্রত্যেক
চরণের শেষ ও শুরুতে অবধি অনুপ্রাস। সেই জন্যই হয়তো বাংলায় এই ছন্দকে আয়ত্ত ও সঠিক
ব্যবহার আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং মনে হল। আমার মনে হয়, সিংহাবলোকন ছন্দ বাংলা
কাব্য-প্রকরণকে সমৃদ্ধই করবে।
প্রশ্ন-২২) মৃগাঙ্ক - পুনরাধুনিক
বলে অনুপম বাবুর যে দাবি সেটা মেনে নিচ্ছ? মনে হচ্ছে ওই গুলি কবিতা?
জুবিন ঘোষ – এক্ষেত্রেও আমি অনুপমের
পুনরাধুনিকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনুপমের কথা যখন উঠলই, তাহলে একটু বেশি কথাই বলতে হয়। অনুপমের সঙ্গে
আমার প্রথম আলাপ ‘দুপুর’ নামক একটা কবিতার মাধ্যমে। ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল
২রা আগস্ট, ২০০৫। ভালো কবিতা বরাবর আমি সংগ্রহে রাখি, সেই সূত্রেই অনুপমের ‘দুপুর’ কবিতাটা আজও আমার সংগ্রহে
আছে। (সঙ্গে স্ক্যান ছবি দিলাম)। কী অসাধারণ কবিতা ! অনুপম লিখছে, “ঝকঝকে আকাশ থেকে অলক্ষ্যে
ঝরে পড়তে থাকে / অন্ধকারের অদৃশ্য কণাগুলো রোদের ফাঁক দিয়ে”—পরের লাইনটা আরও
সুন্দর, “রোজ দু’টোর সময় একটি সন্ধে আমার বিছানায় ঘুমোতে আসে / সাইকেল চড়ে”। এই দৃশ্যকল্পের জন্য আমার
সমসাময়িক কবি অনুপম তখন থেকেই যেন আমার মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আমার চেয়ে
অনুপমকে আর কেউ বেশি পড়েছে বলে জানি না। আমার নিঃশব্দেই পড়া অভ্যেস। একজনই আমার
চেয়ে বেশি পড়তে পারে, সে

হল অনুপমের সহধর্মীনী। অনুপমের
কবিতায় একটা flourish থাকে । একটা সিনেমেটিক অ্যাকশন ভিউ – যেখানে অখ্যানের ধারাবাহিকতার বদলে দেখতে পাই
খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের কোলাজ বা ভিডিওগ্রাফি যা চিত্রকল্পের বিকল্প নয় বরং চিত্রের
বিবরণ। এই টুকরো সিনারিয়গুলো যেমন একসঙ্গে কথা বলে তেমনি আলাদা
আলাদাভাবেও কথা বলার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। খুব গভীরভাবে
যদি অনুপমের কবিতা পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে প্রত্যেকটা কবিতার শেষেই তথাকথিত
চক্রাকার স্থিরীকৃত বক্তব্য নয় বরং ওপেন-এন্ডেড জার্নি পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই
কবিতাটা শেষ, তারপরে কিন্তু কোনও রিফ্লেকশন নেই। অনুপমের অসাধারণত্ব – প্রথমতঃ ) সিম্বোলিক
রিপ্রেসেনটেশন । দ্বিতীয়তঃ ) সফল ওপেন-এন্ডেড জার্নি – শুরু ও শেষহীন এই
কবিতাগুলোর শব্দ মধ্যস্থিত নৈঃশব্দ্য বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ( যা কিনা Hyper
Reality বৈশিষ্ট্যে কবিতা পাক্ষিক
পত্রিকার আমদানী করা পোস্টমর্ডানিস্ট ধারার সঙ্গে মিলে যায়। ) তৃতীয়তঃ ) একটি পঙ্ক্তিতে একটি মাত্র শব্দ রেখে আপাতভাবে তাকে গুরুত্ব
দেওয়া। সুতরাং
এখানে ভাবার অবকাশও থাকছে, কে আসলে কবিতার কেন্দ্রবিন্দু, না কি কেন্দ্রবিন্দু
বলেই কিছু নেই, নির্বিষয়ী ! –- যেটাকে Hyper content বলতে পারি ( যা কিনা Circumcontentive Poetry বা পরিবিষয়ী কবিতার মূল বিশিষ্টতা। এখানে একটি ভাবার বিষয় পোস্টমর্ডানিস্টদের বিন্দুস্বরণ
তত্ত্বও এর কাছাকাছি আসে)।
অনুপমের উপর একটাই আমার তীব্র
অভিমান। একটি সংখ্যায় অনুপম বাক্ এর জন্য আমার কবিতা আমন্ত্রণ করে নিয়েছিল। আমি
কয়েকটি কবিতার সঙ্গে একটি ছন্দের কবিতা দিয়েছিলাম। সেটিতে অনেকে অনেক কথা বলে,
কিন্তু অনুপম তার সম্পাদিত বাক্-এর কমেন্ট বক্সে এসে জানায় যে নেহাতই আমন্ত্রণ
করে নিয়েছিল বলে এই কবিতা তাকে প্রকাশ করতে হয়। একজন সম্পাদক হিসেবে আমন্ত্রিত
কবিতার কমেন্ট বক্সে এসে এই কথা বলায় আমি ক্ষুদ্ধ ও অপমানিত হয়েছিলাম। এটা সদভিপ্রেত
সৌজন্য হয়নি বলেই মনে হয়েছে। অনুপম আমার বন্ধু, ছন্দ কবিতা পছন্দ না হলে, আগেই অন্য কিছু চেয়ে নিতে পারত। এরপর
অনুপমও আমার কবিতা চায়নি আমিও দিইনি। আমি পত্রিকার লেখার বৈশিষ্ট্য দেখে কেন দেব?
তাহলে আমার নিজস্বতা কোথায়? যাইহোক আমি কিন্তু অনুপমের পুরোনো লেখাগুলোর যথেষ্ট
অনুরাগী এখনও।
একসময় অনুপমের কবিতায় ডটের ব্যবহার
নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলাম। তখন ২০১২ হবে। ভেবেছিলাম, এই ২০১২তে কেনই-বা এত ডটের
ব্যবহার রাখব । গতিশীলতা বোঝাতে শব্দই তো যথেষ্ট এই কথা তো অনুপম আগেই বুঝেছে। আবার একটা সময় আমি দেখেছিলাম,
ইটালিয়ান চিত্র পরিচালক ও কবি পিয়ের পাওলো পাসোলিনিকেও যেমন অনুপম কবিতার বিষয় করে
ফেলতে পারে তেমনি, ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত চিত্রকর Rembrandt Harmenszoon van Rijn-ও হয়ে উঠতে পারেন অনুপমের কবিতার বিষয়। পুরাধুনিক পর্বের আগের
অনুপমের ‘হাইওয়ে’ কাব্যগ্রন্থটিতে যখন টুসকিকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলো পড়েছিলাম
সেখানে কবিতার মধ্যে কিন্তু ব্যাপ্তি ও চিরকালীনতাটা ছিল। সঙ্গে বহমানতার
আকস্মিক বাঁকে আনএক্সপেক্টেড সাসপেন্স। আবার ‘অনুপম % মানুষেরা’ কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু
কবিতায় পেয়েছিলাম অসাধারণ কিছু চিত্রকল্প – “তিনটে ফুটকি দিলেই চাঁদ পৃথিবী সূর্যকে একই লাইনে বসিয়ে
দেওয়া যায়” কিংবা “জামপাতায় ঠিকরে আসছে জামরুলপাতার রোদ”। ডট ভিন্ন আর কোনও যতিচিহ্ন
অনুপম ব্যবহার করেনি। সেই অনুপমকে আমি কিন্তু হারিয়ে ফেললাম।
 এবার পুনরাধুনিক বিষয়ে
কথা, আগেই বলি, যে কোনও নতুন কিছু স্বাগত। ঢেউয়ের বিপরীতে গেলে নৌকো ডুববার আশঙ্কা
তো থেকেই যায়, তবুও স্রোতের বিররীতে না গেলে স্থবিরতা থেকে মুক্তির পথ নেই।
অনুপমকে এখানেই স্বাগত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা এই কারণে দিতে ইচ্ছে হয় যে সে এই ঢেউয়ের
বিপরীতে যাবার প্রত্যয় অর্জন করেছে। সেই কারণেই কবিতার অপরাপর আন্দোলন ও ধারাগুলির
মতো এক্ষেত্রেও অনুপমের নবনির্মিত ধারার প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল। তবুও সমসাময়িক কবি
হবার দৌলতে ও অন্যতম তার ভালো পাঠক হবার জন্যই আমার কিছু বলার অধিকার ভেবেই
দু-চারটে কথা বলব। আগে তবু দেখতাম আংশিক নির্বিষয়ী হয়েও অনুপম শেষপর্যন্ত কবিতার
কেন্দ্রমুখীন ভাবনায় ফিরে আসত। অর্থাৎ অনুপম আগে পুরোপুরি কেন্দ্রবিমুখীনতার দিকে
যেতে পারেনি। পরবর্তী অনুপমের লেখার চরিত্র পুনরাধুনিক পর্বে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে,
নির্বিষয়ী আরও অস্পষ্ট হচ্ছে, লজিক্যাল ক্লেফটে অর্থাৎ যুক্তিফাটলে মাত্রাতিরিক্ত
চির লক্ষ্মণীয়, শব্দের মধ্যস্থিত ইন্টারলকড্ আরও বেশি গা ছাড়া যেন ‘কিচ্ছু হয়নি’ এমনটি ভাব নিয়ে দিব্যি হাসি-হাসি
মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধ্বনিপ্রধান কবিতায় তারই মাঝে কিছু কবিতা চিলিক দিয়ে ওঠে। এই
পর্বে অনুপমের কবিতায় অতিরিক্ত পরিমিতি কবিতাকে উদার হতে দেয় না। যেন মন খুলে কথা
বলতে পারছে না। যে কোনও শিল্পই কিন্তু একটা বিকল্প কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ।
যুবতীর মেদহীনতা ভালো কিন্তু অতিরিক্ত মেদহীন হলে কেমন দেখাবে বলো তো? Cathie Jung নামের সেই ভদ্রমহিলার মতো দেখতে লাগবে যার কিনা মাত্র ১৫
ইঞ্চি পেট ও কোমর (সঙ্গের ছবি) ।
এবার পুনরাধুনিক বিষয়ে
কথা, আগেই বলি, যে কোনও নতুন কিছু স্বাগত। ঢেউয়ের বিপরীতে গেলে নৌকো ডুববার আশঙ্কা
তো থেকেই যায়, তবুও স্রোতের বিররীতে না গেলে স্থবিরতা থেকে মুক্তির পথ নেই।
অনুপমকে এখানেই স্বাগত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা এই কারণে দিতে ইচ্ছে হয় যে সে এই ঢেউয়ের
বিপরীতে যাবার প্রত্যয় অর্জন করেছে। সেই কারণেই কবিতার অপরাপর আন্দোলন ও ধারাগুলির
মতো এক্ষেত্রেও অনুপমের নবনির্মিত ধারার প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল। তবুও সমসাময়িক কবি
হবার দৌলতে ও অন্যতম তার ভালো পাঠক হবার জন্যই আমার কিছু বলার অধিকার ভেবেই
দু-চারটে কথা বলব। আগে তবু দেখতাম আংশিক নির্বিষয়ী হয়েও অনুপম শেষপর্যন্ত কবিতার
কেন্দ্রমুখীন ভাবনায় ফিরে আসত। অর্থাৎ অনুপম আগে পুরোপুরি কেন্দ্রবিমুখীনতার দিকে
যেতে পারেনি। পরবর্তী অনুপমের লেখার চরিত্র পুনরাধুনিক পর্বে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে,
নির্বিষয়ী আরও অস্পষ্ট হচ্ছে, লজিক্যাল ক্লেফটে অর্থাৎ যুক্তিফাটলে মাত্রাতিরিক্ত
চির লক্ষ্মণীয়, শব্দের মধ্যস্থিত ইন্টারলকড্ আরও বেশি গা ছাড়া যেন ‘কিচ্ছু হয়নি’ এমনটি ভাব নিয়ে দিব্যি হাসি-হাসি
মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধ্বনিপ্রধান কবিতায় তারই মাঝে কিছু কবিতা চিলিক দিয়ে ওঠে। এই
পর্বে অনুপমের কবিতায় অতিরিক্ত পরিমিতি কবিতাকে উদার হতে দেয় না। যেন মন খুলে কথা
বলতে পারছে না। যে কোনও শিল্পই কিন্তু একটা বিকল্প কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ।
যুবতীর মেদহীনতা ভালো কিন্তু অতিরিক্ত মেদহীন হলে কেমন দেখাবে বলো তো? Cathie Jung নামের সেই ভদ্রমহিলার মতো দেখতে লাগবে যার কিনা মাত্র ১৫
ইঞ্চি পেট ও কোমর (সঙ্গের ছবি) ।
পুনরাধুনিক পর্বে অনুপমের কবিতায় শব্দের ব্যবহার অনেকটা
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের
ব্যবহারের মতো। কবিগুরুর হাতে একটিমাত্র তুলি, ও
তাঁকে যে রঙের পাত্রই এগিয়ে দেওয়া হত সেই রঙের মধ্যেই তুলি ডুবিয়ে দিতেন। রং
নির্বাচনে সময় বা ধৈর্যের পরোয়া করতেন না। অনুপমের শব্দের ব্যবহারও পুনরাধুনিক
পর্বে সেইরকম মোড় নিয়েছে।
পুনরাধুনিক শব্দটি সেই পুনরাবৃত্তির দিকেই চলে যাচ্ছে। এইখানে নতুন অনুপমের
সঙ্গে আমার সামান্য তাত্ত্বিক ডিফারেন্স রচিত হতে পারে। অনুপম কি দাবী করবে, যে
অনুপম যে আঙ্গিক বেছে নিচ্ছে তা আগে কখনও লেখা হয়নি ? পুনরাধুনিকের আঙ্গিকে অনুপম স্তবক
বা লাইনের শেষে নিচে নিচে দাঁড়ি রেখে দেওয়া। কবি পুস্কর দাশগুপ্ত, অনন্ত দাশ,
মৃণাল বসুচৌধুরীদের শ্রুতি আন্দোলনেও দেখা গেছিল ‘নতুন ধরনের মুদ্রণবিন্যাসের
সাহচর্যে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি’ করা। এখানেও তো নতুন ধরনের
মুদ্রণবিন্যাসের সাহায্য নেওয়া হল। দৃষ্টিগ্রাহ্য করাটাই মূল উদ্দেশ্য। কবিতার স্তবক
বা পঙ্ক্তির নিচের উলম্ব রেখাটির আর কোনও প্রয়োজন আছে কি ! শব্দের মত তারাও কি
অর্থবহ ! এছাড়াও পুনরাধুনিকের আঙ্গিকে অনুপম কোথাও কোথাও শব্দটি লিখে তাকে
পেটবরাবর কেটে দেয়। এটাও তো নতুন নয়। অন্তত পুনরাধুনিক বৈশিষ্ট্য বলে দাবী করা
যাবে না। নয়ের দশকে ১৯৯৬
সালের ১৪ই ডিসেম্বর ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘না-পাঠানো চিঠি’ কবিতায় ( Epistolary আঙ্গিকে লেখা) প্রথমবার কোনও শব্দ লিখে তার পেট বরাবর কেটে
দেওয়া পাই। ‘না-পাঠানো চিঠি’ কবিতায় দশম লাইনেই ‘মা, আমাদের’ দুটি শব্দ লিখে তাকে পেট
বরাবর কেটে দেন ‘মা, আমাদের’ সুনীল দা। পরের লাইনটাই যেন শুধরে লিখলেন তিনি, “মা, তোমাদের ঘরের চালে নতুন
খড় দিয়েছো ?” –- যেন ‘আমাদের’ শব্দটা কেটে দিয়ে সেই ঘর কতটা পর হয়ে গেছে সেটাই
বুঝিয়েছিলেন সুনীল দা। আবার ওই একই কবিতায় ৪৫তম পঙ্ক্তিতে একইভাবে লিখলেন, “আমাদের তোমাদের গ্রামে পটল
পাওয়া যায় না” – আবার ৮১তম

পঙ্ক্তিতে পুনরায় এই মুদ্রণবিন্যাসের সাহায্য
নিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, “খুব ইচ্ছে হলো, একবার আমাদের বাড়িটা দেখে আসি”— সুতরাং দেখা
যাচ্ছে, এই আঙ্গিকটিও সুনীল গাঙ্গুলীর একটি বিখ্যাত কবিতায় ব্যবহৃত, বাংলা কবিতায়
নতুন আমদানী নয়। (পরবর্তীকালে এই আঙ্গিকটা সুনীলের শ্রেষ্ঠ কবিতায় বির্জিত হয়েছে
কোনও এক অলীক কারণে, হয়তো প্রুফ রিডার মাঝখান বরাবর কাটা-টা বুঝতে পারেননি,
ভেবেছিলেন হয়তো সুনীলবাবু লাইনটি বর্জন করেছেন, তাই কেটে দিয়েছেন, সুনীলদাও নিশ্চই
সময় করে এটা খেয়াল করে দেখেননি। এখন সুনীলদা মারা যাবার পর সেই কারণটা জানার আর
কোনও উপায় নেই)। দেখা গেল, সুনীল দার একটি সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল পেট বরাবর
এইভাবে কাটবার। অনুপমের লেখার এই
বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও কোনও সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় থাকুক সেটাই আমি চাইব। আমার সাজেশন
হল, অনুপম অন্তত এটা বলুক যে আদি খসড়া আর মূল আফটার এডিটেড ভার্সানকে পাশাপাশি
রেখে দেবার এটা একটা চমৎকার উপায় হতে পারে, সুনীলেরও তো তাই ছিল ! Epistolary আঙ্গিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে উলম্ব রেখাগুলি আমার
কাছে অন্তত যুক্তিগ্রাহ্য অর্থবহ করে তুলতে পারছি না, বারবার শ্রুতির
দৃষ্টিগ্রাহ্য করার যুক্তির দিকেই তা ঠেলে দিচ্ছে। তাহলে তো পুনরাধুনিক আর
পুনরাধুনিক থাকল না এটাই যা! এটা কিন্তু আক্রমণ না, সমসাময়িক কবির প্রতি মুখোমুখি
বসে তাত্ত্বিক আলোচনাই ধরে নাও। অনুপম আমার পরম বন্ধু।
প্রশ্ন-২৩) মৃগাঙ্ক - তুমি তো
আমার কোন সিনেমাই দেখোনি। তাও ভরসা রাখছ কি করে?
জুবিন ঘোষ – তোমার ছবি দেখার তেমন
সৌভাগ্য হয়নি বলে নিজের মনের মধ্যে একটা গভীর আফসোস তো আছেই। তবে যেগুলো দেখেছি
অর্থাৎ ‘মেঘ বলেছে জলকে চলে মেয়ে’ আবৃতি –এর যে ভিডিওগ্রাফি দেখেছি তা
আমার খুব ভাল লেগেছিল, বাবা নামক গানটার যে দৃশ্যায়ন দেখেছিলাম সেই কাজটা আমার
অসাধারণ লেগেছিল, তোমার সঙ্গে প্রশান্ত বলে কেউ বোধহয় ছিল। সেখানে একটা ভাঙা
পলেস্তরা-খসা দেওয়ালের সামনে দিয়ে কয়েকটা পেন্টিং নিয়ে যাবার দৃশ্য ছিল, পরে সেটা
ফেলে দেওয়া হচ্ছে, অর্থবহ লেগেছিল দৃশ্যটা। অচলায়তন আমার এখনও দেখা হয়নি। ইতি অপুতে হাতের ওপর আর
জ্বলন্ত প্রদীপগুলো পর পর রাখার একটা চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে, জ্বলা নিভে যাবার আগেই
আর একটা জ্বলুনি ওভারল্যাপ করার দৃশ্য – প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতোরের অনুপ্রেরণায় যেটা
বানিয়েছিলে সেই অসামান্য কাজটা আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না। সেখানে দেখেছিলাম
তোমার ভাবনার ধ্রুপদী দিকগুলো ফুটে উঠেছিল তাতেই। এইগুলো দেখেই তো তোমার উপর ভরসা
করতে ইচ্ছে হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের একশ বছর হয়ে গেল। এবার তো তোমাদের আসার পালা,
সেই দিকেই তো যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা।
প্রশ্ন-২৪) বাক্ ব্লগজিন - দৃশ্যে কবিতা বলার
প্রয়োজন হবে কেন? ভাষা কি কোথাও
গিয়ে আটকে যাচ্ছে, এগোতে পারছে না
বলে মনে হয়?
জুবিন ঘোষ – আলোর গতি সবসময়তেই বেশি।
বাজ পড়লে আগে আমরা আলো দেখতে পাই তারপর শব্দ আসে। কবিতায় যাই লেখ না কেন বাস্তব
অনুভূতি দৃশ্যে অনেক স্পষ্ট। আমার মনের মধ্যেও এমন অনেক দৃশ্য দানা বেঁধে আছে যাকে
কখনও কখনও আপাত অসংলগ্ন বলে মনে হয়। তাকে মূর্ত করার লোভ এখনও ভেতরে ভেতরে জিয়িয়ে
রেখেছি।
প্রশ্ন-২৫) বাক্ ব্লগজিন - না
আমি আমার সিনেমার কথা বলছিলাম, যেগুলি এখনো
অনলাইনে আসেনি। তাই অবাক হয়েছিলাম। যাই হোক পরের প্রশ্নে আসি, অনেকসময় এরকম হয়, কারো প্রতি ব্যক্তিগত অভিমান, তার শিল্পের
প্রতিও অভিমানের জন্ম দেয়। তার শিল্পকে আক্রমণ করতে থাকে 'মানুষ'টি। আবার অপর
পক্ষে তোষামোদকারীর শিল্পের বাহবা দিতে থাকে। এরকম কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে? তুমি বিষয়টিকে কোন চোখে দেখ ?
জুবিন ঘোষ – এমন ঘটনা তো অহরহ ঘটছে। ‘যাকে দেখতে নারি, তার চলন
বাঁকা’। প্রকৃত শিল্পীরা কিন্তু এটা করে না। তোষামোদকারীর শিল্পের বাহবার ফলে হতাশায়
প্রকৃত শিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছে, আসলে শিল্পের প্রতি সততা থাকাটা খুব দরকার। এই যে
জয় গোস্বামীকে দেখো, তাঁকে তোষামোদকারীর কিন্তু অভাব নেই, তবুও গোঁসাইবাগানে দেখতে
পাই তিনি তাঁর সব থেকে কাছের দুই কবির কবিতা সম্পর্কে একটা কথাও লেখেননি সাত বছরে।
প্রকৃত শিল্পের কদর করেছেন সেখানে। মুশকিল হচ্ছে অনেক অগ্রজ কবিই এগুলো দেখে
শিক্ষা নেন না। এখন দেখতে পাই একটি বিখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনে তোষামোদকারীদের
বাড়বাড়ন্ত কতটা হয়েছে। এর ফলে কী হয় জানো ? নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়, আর ভবিষ্যতে
কবিটির বা সম্পাদকটির বা আলোচকটির কাজের অথেন্টিকেশন এবং বিশ্বাসযোগ্যতাও কমে যায়।
আর তোষামোদ প্রিয় তারাই হয় যাদের নিজেদের কিছু দেবার নেই, নিজের উপর বিশ্বাস নেই
বলেই দল বাড়িয়ে নিজেদের সেভ রাখতে চায়, যেন ব্যাপারটা এইরকম, দেখ আমার অনেক
ফলোয়ারস্ আছে টাইপের একটা মেকি আবহ তৈরি করে নিজেদের চারপাশে। ফলোয়ারস্ বা তোষামোদকারী
আছে ঠিক কথাই, পাঠক আছে কি ? (প্রকৃত পাঠকের কথা না হয় ছেরেই দিলাম।) :P তবে আমি
দুএকজন কবির নাম বলতে পারি যারা এই তোষামোদের বাইরে বর্তমানে ভীষণভাবে নিরপেক্ষ,
যেমন, সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, জয় গোস্বামী, শ্যামলকান্তি দাশ, মৃদুল
দাশগুপ্ত, রামকিশোর ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি দাশ, উজ্জ্বল সিংহ, শ্রীজাত, বিনায়ক
বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন, পৌলমী সেনগুপ্ত, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতুল
দত্ত, গৌতম মণ্ডল, গৌরাঙ্গ মিত্র, নাসের হোসেন, শংকর চক্রবর্তী, অলোক বিশ্বাস, অলক
বিশ্বাস। আর এই সাক্ষাৎকারটা কিছু না বাদ দিয়ে ছাপলে নতুন অনুপমকেও এই তালিকায়
রাখতে বাধ্য হব।
(অনুপম মুখোপাধ্যায়ের কথা : জুবিন এখানে যতটা সম্মান বজায় রেখে কথা বলেছে, 'লিপি' পত্রিকায় আমার কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ও সেটা করেনি। সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষোভ আর রোষের চিহ্ন ছিল। সম্ভবত, যেমন নিজেই বলছে, 'বাক'-এ কবিতা দিয়ে সুখকর অভিজ্ঞতা পায়নি (ওর ছন্দে ভুল ছিল। আমি আনএডিটেড ছেপেছিলাম কারন ও আমন্ত্রিত ছিল। পাঠক সেই প্রসঙ্গ তুলতে বলেছিলাম আমন্ত্রিত কবির ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা আমি সম্পাদনা বা প্রত্যাখ্যান করিনা। অবিকৃত ছাপি।), তাই চটে গিয়েছিল। ও পরিণত হচ্ছে। যাই হোক, আমাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ায় আমি সম্মানিত। ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কেটে দেওয়া শব্দের প্রসঙ্গ তুলেছে। সেটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও প্রথম করেননি সম্ভবত। পরে ওই কবিতা কি গ্রন্থিত হয়েছিল? যদি না হয়, ওই কবিতাকে আমরা সুনীলের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত না-ও ভাবতে পারি। ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র। আমি নিজে ওই কবিতাটি আজই প্রথম পড়লাম। খুবই রদ্দি লেখা। সুনীলের প্রতিনিধিত্ব ওতে নেই। 'আমাদের' শব্দটা কেটেছেন, শুধু ব্যক্তিগত সুরে, না কাটলেও কিছু যেত আসত না। অনেক কবি অনেক কিছুই করেন, পরে সেটাকে পাগলামি বা খেয়াল ভেবে আর স্বীকৃতি দেননা। এ কি সম্ভব যে আমার আগে এমনকি সুনীলের আগে পৃথিবীর কোনো কবি ভাবেননি তাঁর বাতিল করা শব্দগুলোকেও কবিতায় রাখলে কেমন হয়? বা, অনেকগুলো সম্ভাবনায় যদি পাঠককে ওভাবে নিয়ে যাওয়া যায়? অনেকে তো নিজের হাতের লেখা পান্ডুলিপিকেও বই করেছেন। আমি নতুন কিছু করছি না। কিন্তু কেন শব্দগুলোকে কেটে দিচ্ছি তার উত্তর আমার সদ্য প্রকাশিত বইটিতে আছে। জুবিন শ্রুতি কবিতার প্রসঙ্গ তুলেছে। এগুলো নতুন নয়, আমার কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকেই এই প্রসঙ্গগুলো তুলে থাকেন। আসলে এগুলো একটা কৌশল- ''আরে এ তো আগেও একবার হয়েছে, সেই যে অমুকের সেই কবিতাটায়, এ আর এমন কী, পিঁপড়ের পাখা কেন গজায় সকলেই জানি!'' শ্রুতি কবিতার সঙ্গে আমার কবিতার বা ভাবনার সাদৃশ্য শ্রুতি কবিরাও স্বীকার করবেন বলে মনে হয়না, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী বা পুষ্কর দাশগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। আমি উত্তর পাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। সবচেয়ে বড় কথা, পত্রপত্রিকার লেখা পড়ে কি হবে কিছু? ওই মেয়েটির ছবি খুব আপত্তিকর, ওটা ব্যবহার করে মেয়েদের সম্মান বাড়ল না, কারন কবিতা তো নারীদেহ নয়, রম্যতার আবাস নয়, মেয়েদের শরীরও শুধু রম্যতার আবাস নয়, যে যার নিজের মতো নিজের শরীর সাজাবে, ঋতুপর্ণ ঘোষ তো পুরুষদেহটাই পছন্দ করেননি নিজের, নারী হতে চাইলেন, রম্যতায় নয়, স্বভাবে। পুনরাধুনিক বিষয়ে কথা বলার আগে আমার 'প্রকল্প ও স্ফটিক' কাব্যগ্রন্থটি সম্ভবত পড়ে নেওয়া ভালো। সামগ্রিক ধারণাটায় এসো জুবিন। নাহলে কথা বলার অর্থ থাকে না। আঙ্গিক আর ভাবনার ভেদ ও অভেদের জায়গাটা ধরতে হলে বইটা পড়তে হবে। আমি একবারও বলিনি আমি যে কবিতায় শব্দ কেটে দিচ্ছি, আমিই পৃথিবীতে প্রথম করছি, বা আমিই প্রথম কোনো দাঁড়িকে তার জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে গেলাম। দাঁড়িটা তার নিজের জায়গায় থাকলে কি তা আমার নিজস্বতা হত? হত না। আমি সেটাই করতাম যেটা এখন ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জন কবিতালেখক করছেন। এটাতেও হয়ত হচ্ছে না, কিন্তু আমি আমার পছন্দসই জায়গাটা পাচ্ছি এবং নিজের সিদ্ধান্তটা জনসাধারণের বাইরে থেকে দেখাতে পারছি, ১০১ তম কবিতালেখক হিসেবে নিজের কাজতা করছি। আজ থেকে ৩০০ বছর আগেই কেউ করে থাকতে পারেন। ফ্রান্সে কেউ করতে পারেন। আমেরিকান কোনো কবি করে থাকতে পারেন। তাতে কিছু আসে যায়না। কারন আমি তেমন কোনো কবিকে আজও পড়িনি। ফলে আমি কাউকে অনুসরণ এমনকি অনুকরণ করছি না। তালপাতার পুথির যুগে গেলে তো পেয়েই যাবে কিছু উদাহরণ, সেখানে কিছু শব্দ তো কাটাই পড়ত, আমি নিজে ওখান থেকেই ধারণাটা পেয়েছিলাম। আজ যদি কেউ অক্ষরবৃত্তে লেখেন, তাহলে তো বলতে হয় লিখো না, জীবনানন্দ দাশ করে গেছেন। এগুলোতেই পুনরাধুনিক শুরু ও শেষ হয়না। পুনরাধুনিক একটা ভাবনা। আর ওগুলো আমার আঙ্গিকের অংশ। আমি যদি শব্দ না কাটতাম, তাহলে কি আমার আঙ্গিকের নিজস্বতা বাড়ত, ও ঠিক এতগুলো কথাই আমার কবিতা নিয়ে বলত? ঠিক যেমন কমা, দাঁড়ি ঠিক জায়গায় থাকলে, সেটাও আঙ্গিকগত একটা সিদ্ধান্ত হত যা বাকি সবাইকে অনুসরণ করত, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজেই জানতে পারতাম না। আমি একটু নিজেরই অভ্যাসের বাইরে গেলাম, পাঠকেও যেতে অনুরোধ করলাম। এগুলো আমার কবিতার একটা আঙ্গিকে সাহায্য করে মাত্র, যা আমি আমারই বিবিধ চিন্তাসূত্র থেকেই পেয়েছি, এবং পাওয়াটা একেকটা আবিষ্কার আমার কাছে। আমি বিশ্বাস করি, পুনরাধুনিক কবিতায় বাংলা কবিতার সামগ্রিকতা একটা আবহাওয়া হিসেবে বিরাজ করবে। সেখানে কাটা শব্দের জায়গা যেমন আছে, যদিও বাংলা কবিতায় তার জায়গা কবে প্রথম তৈরি হয়েছে তা অমূলক, পয়ারেরও আছে, অনুপ্রাসেরও আছে, যমকেরও আছে, আবার সিনেমা বা সঙ্গীতেরও আছে, এমনকি নাচের। সেখানে আধ্যাত্মিকতা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা ধ্বনিগুণ। সেখানে ঈশ্বর গুপ্ত আর পরেশ মন্ডল সকলেই আছেন। সর্বোপরি আছেন রবীন্দ্রনাথ। গুস্তাখি মাফ হোক, একটু আত্মশ্লাঘা করে ফেললাম। শাস্ত্রানুসারে একটু মরে গেলাম ভাই। আর এবারের সাক্ষাৎকারের ভাষাটা গতবারের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। প্রায় এক অন্য জুবিন সাক্ষাৎকার দিয়েছে মনে হচ্ছে। অভিনন্দন রইল। )
 এবার পুনরাধুনিক বিষয়ে
কথা, আগেই বলি, যে কোনও নতুন কিছু স্বাগত। ঢেউয়ের বিপরীতে গেলে নৌকো ডুববার আশঙ্কা
তো থেকেই যায়, তবুও স্রোতের বিররীতে না গেলে স্থবিরতা থেকে মুক্তির পথ নেই।
অনুপমকে এখানেই স্বাগত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা এই কারণে দিতে ইচ্ছে হয় যে সে এই ঢেউয়ের
বিপরীতে যাবার প্রত্যয় অর্জন করেছে। সেই কারণেই কবিতার অপরাপর আন্দোলন ও ধারাগুলির
মতো এক্ষেত্রেও অনুপমের নবনির্মিত ধারার প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল। তবুও সমসাময়িক কবি
হবার দৌলতে ও অন্যতম তার ভালো পাঠক হবার জন্যই আমার কিছু বলার অধিকার ভেবেই
দু-চারটে কথা বলব। আগে তবু দেখতাম আংশিক নির্বিষয়ী হয়েও অনুপম শেষপর্যন্ত কবিতার
কেন্দ্রমুখীন ভাবনায় ফিরে আসত। অর্থাৎ অনুপম আগে পুরোপুরি কেন্দ্রবিমুখীনতার দিকে
যেতে পারেনি। পরবর্তী অনুপমের লেখার চরিত্র পুনরাধুনিক পর্বে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে,
নির্বিষয়ী আরও অস্পষ্ট হচ্ছে, লজিক্যাল ক্লেফটে অর্থাৎ যুক্তিফাটলে মাত্রাতিরিক্ত
চির লক্ষ্মণীয়, শব্দের মধ্যস্থিত ইন্টারলকড্ আরও বেশি গা ছাড়া যেন ‘কিচ্ছু হয়নি’ এমনটি ভাব নিয়ে দিব্যি হাসি-হাসি
মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধ্বনিপ্রধান কবিতায় তারই মাঝে কিছু কবিতা চিলিক দিয়ে ওঠে। এই
পর্বে অনুপমের কবিতায় অতিরিক্ত পরিমিতি কবিতাকে উদার হতে দেয় না। যেন মন খুলে কথা
বলতে পারছে না। যে কোনও শিল্পই কিন্তু একটা বিকল্প কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ।
যুবতীর মেদহীনতা ভালো কিন্তু অতিরিক্ত মেদহীন হলে কেমন দেখাবে বলো তো? Cathie Jung নামের সেই ভদ্রমহিলার মতো দেখতে লাগবে যার কিনা মাত্র ১৫
ইঞ্চি পেট ও কোমর (সঙ্গের ছবি) ।
এবার পুনরাধুনিক বিষয়ে
কথা, আগেই বলি, যে কোনও নতুন কিছু স্বাগত। ঢেউয়ের বিপরীতে গেলে নৌকো ডুববার আশঙ্কা
তো থেকেই যায়, তবুও স্রোতের বিররীতে না গেলে স্থবিরতা থেকে মুক্তির পথ নেই।
অনুপমকে এখানেই স্বাগত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা এই কারণে দিতে ইচ্ছে হয় যে সে এই ঢেউয়ের
বিপরীতে যাবার প্রত্যয় অর্জন করেছে। সেই কারণেই কবিতার অপরাপর আন্দোলন ও ধারাগুলির
মতো এক্ষেত্রেও অনুপমের নবনির্মিত ধারার প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল। তবুও সমসাময়িক কবি
হবার দৌলতে ও অন্যতম তার ভালো পাঠক হবার জন্যই আমার কিছু বলার অধিকার ভেবেই
দু-চারটে কথা বলব। আগে তবু দেখতাম আংশিক নির্বিষয়ী হয়েও অনুপম শেষপর্যন্ত কবিতার
কেন্দ্রমুখীন ভাবনায় ফিরে আসত। অর্থাৎ অনুপম আগে পুরোপুরি কেন্দ্রবিমুখীনতার দিকে
যেতে পারেনি। পরবর্তী অনুপমের লেখার চরিত্র পুনরাধুনিক পর্বে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে,
নির্বিষয়ী আরও অস্পষ্ট হচ্ছে, লজিক্যাল ক্লেফটে অর্থাৎ যুক্তিফাটলে মাত্রাতিরিক্ত
চির লক্ষ্মণীয়, শব্দের মধ্যস্থিত ইন্টারলকড্ আরও বেশি গা ছাড়া যেন ‘কিচ্ছু হয়নি’ এমনটি ভাব নিয়ে দিব্যি হাসি-হাসি
মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধ্বনিপ্রধান কবিতায় তারই মাঝে কিছু কবিতা চিলিক দিয়ে ওঠে। এই
পর্বে অনুপমের কবিতায় অতিরিক্ত পরিমিতি কবিতাকে উদার হতে দেয় না। যেন মন খুলে কথা
বলতে পারছে না। যে কোনও শিল্পই কিন্তু একটা বিকল্প কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ।
যুবতীর মেদহীনতা ভালো কিন্তু অতিরিক্ত মেদহীন হলে কেমন দেখাবে বলো তো? Cathie Jung নামের সেই ভদ্রমহিলার মতো দেখতে লাগবে যার কিনা মাত্র ১৫
ইঞ্চি পেট ও কোমর (সঙ্গের ছবি) ।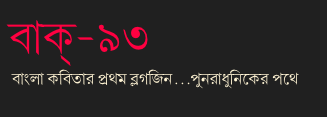













Jubin tomar kabyogrontho alochonar ongso porte khub valo laglo...khub sundar bisleshon chondo nieo...:-)
ReplyDeleteমনোযোগ দিয়ে পড়েছি। ব্যক্তি জুবিন নিজের বোধের কথা বলেছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে, সহমত হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন নেই। পরিচয়ের, জানার প্রক্রিয়া। নিজেকে সুন্দর প্রকাশ করেছে। জুবিনকে বুঝতে পারি।
ReplyDeleteঅনুপম ও জুবিনের প্রসঙ্গটা আরোপিত মনে হয়েছে। পাঠকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উপনিত করা। অহেতুক তাপের সঞ্চার।
আমার অবস্থান ও গন্তব্যের উপরেই নির্ভর আমার গতিমুখ। প্রবাহ এখানে নিরপেক্ষ বলে মনে হয়।
বিষয়টিকে বাদ দিয়ে বলতে চাই - বর্তমান সময়ের দু-জন কবির যথার্থ উপস্থাপনা।
দু-জনকেই ধন্যবাদ।