কবি সুশীল ভৌমিকের পরিচিতিঃ
Tuesday, September 29, 2015
এবারের কবিতা সুর্মা
বিভাগে রাখা হচ্ছে প্রয়াত কবি সুশীল ভৌমিক এর কয়েকটি টুকরো গদ্য, এবং সাক্ষাৎকারের
নির্বাচিত কুচি। এসব দিয়েই তাঁর কবিতা ভাবনার সন্ধান। এরকম আরও কারও কথা আমাদের মাথায় থাকল। (উমাপদ কর, বিভাগীয় সম্পাদক)
কবি সুশীল ভৌমিকের পরিচিতিঃ
জন্ম ২৮ আগস্ট, ১৯৩৮। ময়মনসিংহের
পারুলিতলা। শৈশবে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। প্রথমে রায়গঞ্জে পরে বহরমপুরে বাস। স্কুল কলেজ
বহরমপুরে। জীবিকা, শিক্ষকতা। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক।
১৯৫৭ সালে কলকাতার একটি পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশ। পরে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সম্পাদিত পূর্বাশায় নিয়মিত প্রকাশ। ১৯৭৪ এ বিবাহ। ১৯৭৮ এ পেসমেকার বসে। প্রচার ও
প্রকাশ বিমুখ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আমি, তবু’ প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালে। ২০০৪ এ ‘নির্বাচিত কবিতা’। বাংলা কবিতাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছানোর
তাগিদে সম্পাদনা করেন ‘Poetry International’ এর কয়েকটি সংখ্যা। কমল চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘বাংলা কবিতার ষাটের দশক’ এবং সুব্রত
রুদ্র সম্পাদিত ‘ষাটের কবিতা’য় সংকলিত। আড্ডাপ্রিয়, অনুজ কবিদের প্রকৃত অভিবাবক ও আশ্রয়স্থল। প্রয়াত ২২
অক্টোবর, ২০০৭।
সুশীল ভৌমিক উবাচ
এক
ব্যক্তিগত জীবন ও কবিতায় আমি
পুড়েই যেতে চেয়েছি--- সঠিকভাবে এই ছিল কবিতায় আমার উদ্দেশ্য। আর্টকে ভীষণভাবে
শ্রদ্ধা করেও আমি নিরপেক্ষ, সমৃদ্ধ ও পরিদৃশ্যমান মননবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিতে
পরান্মুখ আগাগোড়াই।
আমি পুনঃমার্জনার পক্ষপাতী ছিলাম
না এজন্যে যে প্রত্যেক মুহূর্তের মানুষ আলাদা, অসত্যের সম্ভাবনাও থেকে যেত না হলে।
তৃতীয়তঃ আমার লেখালিখির ইতিহাস।
আমি কবিতা লিখে কখনও তৃপ্তি পেতাম না। ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। এমন একটি কবিতাই প্রথম
ছাপা হয় কলকাতার একটি পত্রিকায়। পরবর্তীকালে অসংখ্য পত্রপত্রিকা, যাদের প্রচ্ছদ ও
লেখাগুলি এখনো উঁকি মারে--- আমার প্রকাশিত বহু কবিতা সমেত সেগুলো ঝাঁকামুটের মাথায়
তুলে দিয়েছি। না, কোন পান্ডুলিপির নকল রাখার অভ্যেস আমার কোনদিনই ছিল না। ৬০ দশক
থেকে ৭০ দশক পর্যন্ত এইসব কবিতা উচ্ছিষ্ট হবার সুযোগ পায়নি। ...
কথা একটাই I will not rest.
দুই
No boundary eqals no
boundary
--- Roman Jakobson
সুশীল
ভৌমিক
যে
আমেরিকান কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬২-তে এবং সর্বশেষ প্রকাশকাল ১৯৮৩, তা পড়ে
মনে হয়েছে কবি ঠুনকো একটা স্থিরবিন্দুতে পড়ে নেই, অসম্ভব পরিবর্তন ঘটেছে ভেতরে।
যদিও দ্বিতীয়বার সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে কবি সম্পাদক জানিয়েছেন আরও কিছু দুর্ধর্ষ নতুন
কবিকে অন্তর্ভূক্ত করা হল। কবিরা কোন টেক্নিক্যাল কাঠামোর মধ্যে যেমন আবদ্ধ থাকেন
না, তেমনি একটা অজানা সত্যকে আবিষ্কার করেন। বোদলেয়ের এই দুটি দিকের ওপরেই জোর
দিয়েছেন। কোলরিজ বলেছেন truth is
revelation. আবার ক্রোচের মতে Technique is a part of
vision. সুতরাং, কোন একটার গুরুত্ব বেশি নয়। এই আবিষ্কার কথাটি, যা
একটু আগে উল্লেখ করেছি তা শুধু নতুন জগৎকে উন্মোচন করে না, এতদিনকার পবিত্র ও
অলঙ্ঘনীয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, তার fallacy-কেও আক্রমন করে। নতুন সাহিত্যের অন্যান্য শাখার কিংবা আর্টের ক্ষেত্রেও এই
কথাগুলি অবিসংবাদী এবং সমানভাবে প্রযোজ্য। খুব কাছের ব্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর
সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল সমাজ। কিন্তু পেটার তা উল্টে দেন। নন্দনশিল্পের
দায়বদ্ধতা একান্তভাবে শিল্পীর নিজের বিবেকের কাছে। পেটারকে জনৈক ইয়ংম্যান প্রশ্ন
করেছিল ‘উৎকৃষ্ট হবার প্রয়োজন কী আমাদের?’ চটজলদি উত্তর পেটারের ‘কারণ এটাই আমাদের সৌন্দর্য।’ ব্যক্তিতান্ত্রিকতার সপক্ষে ছিলেন
এই তীক্ষ্ণধী লেখক ও সমালোচক ওয়াল্টার পেটার। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, পেটারের
চিন্তাধারাই হুইস্মাস, গঁতিয়ে ও বোদলেয়ারের নিষিদ্ধ ঐশ্বর্যের দিকে মানুষের
চাহিদাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল। এইভাবে অব্যাহত কবিতা, সীমাহীনতার দিকে।
আমার
ব্যক্তিগত ধারণা, শেষ পর্যন্ত কবিতা খুঁজে নেবে এক ভাবগম্ভীর, শিল্পসম্মত নীরবতা।
তিন
(কয়েকটা
প্রশ্নের উত্তরে)
**
কবিতার কেতাবী সংজ্ঞাগুলি এখন অনেকটাই জোলো শোনাবে। রিডিং বলেছেন ভাষার সারাৎসার।
সার্ত্রর কথাই ঠিক, কবিতা ভাষাকে অস্বীকার করে। ‘Poetry
is the case of loser wins’ অথবা ‘a challange to words’---
অনেকটা ছবির মতো। এতে চলে ধ্বংস ও গড়ার কাজ। সুষমার পরিবর্তে অসমতা এর অন্যতম গুণ।
এভাবে কিছুটা বলা যায়। এর কাছাকাছি প্রশ্ন হবে, ছবি কী? চলচ্চিত্র কী? ইংরাজি
শব্দগুলি ব্যবহৃত হলো মূলের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য।
**
মডার্ণ সাহিত্যের আদর্শবাদ বিশেষভাবে বর্জিত। ওর কোন ভিত্তি নেই, নিছক কল্পনা।
কোথায় সাম্য, কোথায় সামাজিক অধিকার? কান্টের ‘Enlightenment’ এর প্রতিবাদ হিসেবে ধরা যায় মার্কুইনের ‘নারকীয়তা’। সুতরাং পোস্টমডার্ণ কবিতা গভীরতাহীন, আদর্শ,
বিশ্বাসহীন, অনেকটা প্যারোডি গোছের। আমি সম্ভবত প্রথম থেকেই এই কবিতা লিখি।
** শুচিবায়ু
নিয়ে কবিতা লেখা যায় না। শব্দ-ভাষা-বিষয় সম্পর্কে গতানুগতিক চিন্তা কবিতার শত্রু।
পিকাসোর একটি ছবিতে নাসারন্ধ্রের অবস্থান অন্যত্র, হৈ চৈ করার কোন কারণ নেই, সরিয়ে
দিয়েছেন মাত্র--- যিনি বিশ্বের অবস্থা দেখে শিল্প থেকে যে কোন কিছুর সাদৃশ্যকে
নির্বাসন দিয়েছিলেন। জীবন থেকে এসবের জন্ম হয়। মন্দকে কোনভাবেই ভাল করা যায় না।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
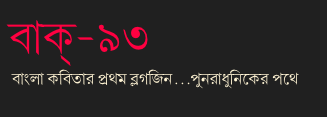









0 comments:
Post a Comment