Tuesday, September 29, 2015
পিপাসা খুলে দ্যায়
পিপাসার দরজা, বন্ধ করবে বলেই
অনুপম মুখোপাধ্যায়
সবেমাত্র হাতে এল অংকুর সাহার
অনুবাদগ্রন্থ ‘অনুসরণকারী’। হুলিও কোর্তাসারের ‘দ্য পারসিউয়ার’-এর
বাংলা করেছেন অংকুর। কাজটা একজন অনুবাদকের জীবনের মাইলফলক যেমন হতে পারে, তাঁর
প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংসও করে দিতে পারে। আমার মতে, অংকুর সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।
খিদেটা যার সত্যিই
পেয়েছে, তিনি তাঁর পাঁউরুটি থেকে ঠিক কতটা বাইরে থাকেন, যখন ভিনদেশি তিনি সেই
বাদামি সুরভিত সুন্দরভাবে তোস্ করা ভিনদেশি রুটিটিকে ভিনদেশি ছুরিতে কাটেন? তিনি
কি ওই রুটির অংশ নন তখন? খিদেই কি রুটি, নাকি রুটিই আসল খিদে? ক্ষুধার্ত নিজেই যদি
একটি রুটি তখন না হন, তবে আর ক্ষুধার বা স্বাদের ভূমিকা কী রইল? কতটা বাইরে থাকতে
পারেন একজন কর্মকর্তা তাঁর কর্মটি থেকে, তিনি কি নিজেকেই করেন না, একা-একা
নির্মাণের যেকোনো কাজের মধ্যেই কি থাকে না স্বমেহন, নিজেকে ফাক্ করার হিংস্রতা?
জীবনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন যতটা যৌনগন্ধী ততটাই জটিল, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এই
প্রশ্ন সংকটজনক, মারাত্মক। একজন শিল্পীর সার্থকতার ধারণা
এই প্রশ্ন থেকে খুব বাইরে নয়, এবং ভিতর তো আমরা দেখতেই পাইনা, কাজেই সার্থকতার
ব্যাপারটা সেখানে, ভিতরে, আমার বাইরে ‘আমি’ হয়ে আছে কিনা কী করে বলি! একজন পুরুষ সহস্র মৈথুনের
পরেও যোনিতে প্রবেশ করতে পায়না, যেন টুথপেস্ট বেরিয়ে আর ঢুকতে পারলনা তার পুরোনো
আশ্রয়ে। সারাটা জীবন সে মা খুঁজে ফেরে, এমনকি নিজের মায়ের মধ্যেও খোঁজে সেই
মাকে... ১০০ % পায়না। একজন কবি বা শিল্পীও তাই।
হুলিও কোর্তাসারের ‘দ্য
পারসুয়ার’ একটি অসামান্য
প্রকল্প এইসব ঘিরেই। একে আপনি নভেলেট বলতে পারেন, বড়্গল্প বলতে পারেন, আবার লেখকের
নিজের মত মেনে নিয়ে ছোটগল্প বলতেও সমস্যা নেই। একটি কাহিনি তার দৈর্ঘ্য দিয়ে এসব
সীমারেখা বাঁধতে পারেনা। আমরা হয়ত ক্রমেই প্রস্তুত হচ্ছি সেই পরিসরের জন্য যখন
একটি উপন্যাস এক পাতার স্পেসে লেখা হবে, আর একটা ছোটগল্প একজন লেখকের জীবনকালকে
অতিক্রম করে যাবে। আজ আর আমরা প্রশ্ন করি কি, এটা ছোটগল্প নাকি উপন্যাস? যারা ওই
প্রশ্নে আজও গেঁথে আছেন, তাঁদের জন্য থাক ক্লাসরুমের বাতাস।
আমি এই লেখাটিকে বরং
একটি প্রজেক্ট বলব।
জ্যাজ সঙ্গীতের জগত
নিয়ে লেখা এই কাহিনিটি। কিন্তু জ্যাজের বদলে লোকগীতি, চিত্রশিল্প, কবিতা, বা
চলচ্চিত্র বা নৃত্যশিল্প হলেও ব্যাপারটা একই হতে পারত। হর্নবাদক জনি কার্টার আসলে
যেকোনো জনি, শিল্পপৃথিবীর যেকোনোজন। তিনি হতাশাগ্রস্ত, আসলে তিনি
উচ্চাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত। মাদক তাঁর আশ্রয়... মদ, হাশিস, হেরোইন। যৌনতা তাঁর অবলম্বন।
একের পর নারী তাঁর জীবনে এসেছে, শুধু নারীর থেকে তাঁর দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে তোলার
জন্যই, কোনো নারীই নিজেকে জনির বাইরে রাখতে পারেনি, অবিশ্যি তাঁর থেকে বেরিয়ে আবার
জীবনে ঢুকতে পেরেছে। একজন নারীর পক্ষে জনি কোনো ব্ল্যাক হোল নন। তিনি এক
অন্য পিকাসো। বহুগামীতা থেকে যে কামশূন্যতা জন্ম নেয়, যে বিবমিষা জন্ম নেয় তার এক
সাব্লিমেটেড আকার এই বুড়ো নিগ্রো হর্নবাদক। কাম তাঁকে আর কিছু দিতে পারবে না, তবু
তিনি নতুন নারীর দিকে যাবেন নিজের পুরোনো অসহায় হাস্যকর শিশ্নটি নিয়ে। নতুন সুরের
দিকে যাবেন, যেমন নিজের চিরপুরোনো বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে। স্যাক্স আর সেক্স তাঁর
জীবনে এক হয়ে যাক, এটা তিনি চাননি, কিন্তু চাইলেই নিজের প্রতি খাঁটি কাজটা করতেন।
পিপাসা তাঁর ঈশ্বর, আমার মনে হয়। ঈশ্বরের নাম গন্তব্য। ঈশ্বরের নাম দরজা। পিপাসা
তাঁর জন্য কদাচিৎ দরজা খুলেছে, কিন্তু শুধু মুখের উপরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই।
কোর্তাসারের চরিত্র জনি
কার্টার সেই অসংখ্য পাশ্চাত্যদেশীয় প্রতিভাদের একজন যারা প্রাচ্যের ছোঁয়া পেলে
বর্তে যেতেন, অমন আধ্যাত্মিকতাশূন্যতায় ঝুলে থাকতেন না। একজন পোস্টমডার্ন মানুষ জনি কার্টার। বিভ্রম
তাঁর জন্মগত পরিসর। প্রতিভা তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে, শান্তি দিতে পারেনি। দরজা তাঁর
সামনে খোলে শুধু নিজেকে বন্ধ করার জন্যই।
আমি জনির মধ্যে নিজেকে
কিছুটা পেয়েছি, আমিও তো পোস্টমডার্ন স্পেসের মধ্যে বেঁচে পোস্টমডার্নকে পেরোতে
চাইছি। তাঁর পরিস্থিতিটা আমারও অতএব। আমার গন্তব্যটা পুনরাধুনিক, যেখানে হেরোইন
নেই, কামস্পর্শহীন যৌনতা নেই। আমি তাঁর হর্নে পেয়েছি আমার কবিতার খাতা। আপনিও
পাবেন, যদি না পান আপনার সৃষ্টির অধিকার নেই, অথবা ‘অধিকার’
শব্দটায় আপনার কোনো গমনাগমন নেই। জনি যে তাঁর হর্ন মেট্রোয় হারিয়ে ফ্যালেন, এই
হারিয়ে ফেলাটুকু আমাদের অনেকেরই সাধ, যেকোনো কালে যেকোনো দেশে, অনেকেরই সাধ্যাতীত।
আমরাও হারিয়ে ফেলতে চাই আমাদের কবিতার খাতা, কিন্তু হারায়না। বরং, আমাদেরই হারিয়ে
দ্যায়। আমরা হয়ে উঠতে পারিনা আমাদের কবিতার খাতা। যিনি হয়ে
উঠতে পারেন, তিনি একজন কালিদাস, শেকসপীয়ার, একজন রবীন্দ্রনাথ।
জনির স্যাক্সোফোন জনি
হয়ে ওঠেনা। অথবা তিনি হয়ে ওঠেন না তাঁর স্যাক্স।
আরেক চরিত্র ব্রুনো।
তিনি সাংবাদিক। বিবাহিত। জনির জীবনীলেখক, কিন্তু ঠিক বসওয়েল বা ডক্টর ওয়াটসন নন।
তাঁর সঙ্গে জনির সম্পর্কটা পারস্পরিক গড়ে নেওয়ার ঝামেলায় ও কোমলতায় ভরে আছে।
ব্রুনোও নারীলোভী। আত্মম্ভরী। আধ্যাত্মিকতাশূন্য। তিনি সঙ্গীতের বয়ন বোঝেন, কিন্তু
আত্মা বোঝেননা। অনির্ণেয়তাকে এড়িয়ে যান। জনির জীবনী লিখছেন ব্রুনো। এই সুবাদেই
জনির জীবনকে তিনি কিছুটা নিজের সম্পত্তি মনে করেন। জীবন আর জীবনীর মধ্যে যে প্রায়
সুর আর স্যাক্সোফোনের দূরত্বই বিদ্যমান, ব্রুনো বুঝতে পারেননা। জনির জীবনকে তিনি
একটা বইয়ের মধ্যে পুরে দিতে চান, একটা বইয়ের চেয়ে বেশি কিছু চাননা জনির জীবন হোক।
কিন্তু ব্রুনো যেমন জনিকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চাইছেন, জনির অসন্তোষ ব্রুনোকে
রেহাই দেয়না, তাঁকে সংক্রমিত করে।
ব্রুনোর লেখা জনির
জীবনী ব্রুনোর তৈরি করা জনির জীবন হয়ে উঠতে চায়। জীবন আর জীবনচরিতের মধ্যে এই এক
অনপনেয় ফাঁক। জনিকে পাবেনা তুমি তাঁর জীবনচরিতে, এবং সেটা সবচেয়ে বেশি বুঝবেন জনি।
মজার ব্যাপার হল, তাঁকে না বোঝার জন্য তিনি তাঁর জীবনীকারকে কথা শোনাতেও ছাড়বেন
না।
তাহলে, কে কাকে অনুসরণ
করছে? কোন জিনিসটার পিছু নিয়েছেন কে?
এই হল ‘দ্য পারসিউয়ার’-এ
হুলিও কোর্তাসারের খেলা। এই হল লীলা।
সদ্য অনুদিত হয়েছে
বাংলায় এই কাহিনি। অনুবাদক অংকুর সাহা। এই প্রজেক্টের অনুবাদ সোজা কথা নয়। যিনি
করবেন, তাঁর শুধু ভাষার দখল যথেষ্ট নয়, হতে হবে একজন পাঠক, সত্যিকারের পাঠক তাঁকে
হতেই হবে। সেইসঙ্গে তাঁর মধ্যে থাকা চাই একজন মৌলিক লেখকের কাঁচা কল্পনাশক্তি যা
অনুবাদের সময়ে তাঁর বোধের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। আবার চাই দর্শনের দৃষ্টি ও ভিত।
অংকুর সাহার মধ্যে এই বিরল ব্যাপার আছে। তিনি নিজে একজন কবিতালেখক। একজন সত্যিকারের
রসিক পাঠক। ফলে কোর্তাসারের মর্মে অংকুর প্রবেশ করতে পেরেছেন, এই কাজটা এই
মুহূর্তে বাংলা দু-তিনজনের বেশি অনুবাদক পারতেন না। খুবই সাবলীল, খুবই বাংলা এবং
আন্তর্জাতিক একটা ভাষা তাঁর আছে। কোর্তাসারের মূল ভাষাটিতে যে আভিজাত্য এবং
বিন্দাস মেজাজ একইসঙ্গে বিরাজ করে, তা তিনি আনতে পেরেছেন।
প্রকাশকের ধন্যবাদ
প্রাপ্য এমন একটি বই বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু অসংখ্য ছাপার
ভুল চোখকে ক্লিষ্ট করে। সম্ভবত প্রুফ দ্যাখার সময় যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। প্রচ্ছদটি
বেশ দায়সারা, এবং হুলিও কোর্তাসারের মলাট হওয়ার উপযুক্ত একেবারেই নয়। প্রকাশক
বইটির প্রতি সুবিচার করেননি, বলতেই হয়। তাঁদের কাছে সম্ভবত হুলিও কোর্তাসার একটা
ব্র্যান্ড, যেমন তসলিমা নাসরিন বা জয় গোস্বামী একটা ব্র্যান্ড। নামটা মলাটে থাকলে
একটা বিশেষ সংখ্যক বই ঠিকই বিক্রি হবে, ভিতরটা যাই হোক। এইসব প্রকাশনা-পত্রিকা
বাইরের পৃথিবীর এই নামগুলোকে ব্যবহার করে, কিন্তু নিজেরা যখন কোনো সাধারণ সংখ্যা
করে, বা কোনো মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশ করে, দ্যাখা যায় গতানুগতিক লেখাকেই
মান্যতা দিয়েছে, কোনোরকম রিস্ক নেয়নি। অবশ্য বর্তমান পরিসরে এসব প্রসঙ্গ তোলার
মানে হয়না, আমাদের অভ্যাস হয়ে যাওয়াই উচিত।
অনুসরণকারী
হুলিও কোর্তাসার
অনুবাদ : অংকুর সাহা
প্রচ্ছদ : অভিজিৎ পাল
প্রকাশক : এবং মুশায়রা
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৫
মূল্য ১৫০ টাকা
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
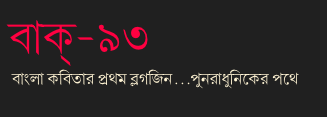










0 comments:
Post a Comment